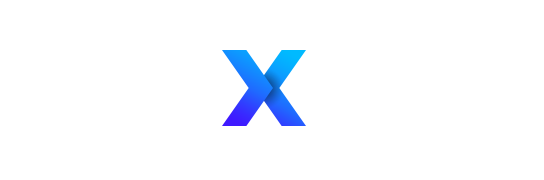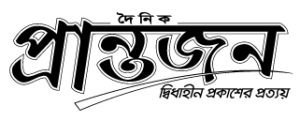মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস আমি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। ওই ৯ মাস আমি যুদ্ধের মাঠেই ছিলাম। ১৯৭১ এর এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় পরিবারের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিই। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জনের এক মাস পর পরিবারের সদস্যদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জন্ম নেয়া ৩ ভাই-বোনসহ আমরা পরিবারের সদস্য ছিলাম ১৩ জন। সদস্যদের মধ্যে থেকে স্বাধীনতার পর আব্বা-আম্মা ও দুই বোন আমাদের ছেড়ে না ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছেন। এর মধ্যে ২০২০ সালে মহামারি করোনার সময় আমাদের সকলের প্রিয়ভাজন ও মানুষের সেবা দিতে যিনি কখনও কাপর্ণ্য করেননি সেই আমার বড় বোন রওশন আরা জোৎস্না আমাদের ছেড়ে যান। ৭১-এ তার জীবন জীবিকাও ছিল দুঃসহময়। আমার সেই বড় বোনকেও প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়েছে নিজের সম্ব্রম ও জীবন রক্ষায়। স্বামী হারা আমার সেই বোন পাকসেনাদের হাত থেকে রেহায় পেতে তার শিশু কন্যাকে নিয়ে গ্রাম গ্রামে পালিয়ে থেকেছেন। সেই বোনের সাথেও আমার সাক্ষাত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের শেষভাগে বগুড়ার বলদিপালান নামের নিভৃত এক গ্রামে।
মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ায় আমাকে আব্বা-আম্মাসহ পরিবারের সকলের সাথে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়েছে নয়মাস। ভারতের বহরমপুর শরণার্থী ক্যাম্পে থাকার সময় পরিবারের সদস্যদের ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে যাই। শরণার্থী ক্যাম্পে আব্বা-আম্মাসহ পরিবারের সবার সাথে এক সাথে শেষ বারের মত খাবার খেয়ে বিদায় নিয়ে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কুড়মাইল মুক্তিযোদ্ধা ইয়থ ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা হই। ওই ক্যাম্প করেছিলেন পাবনার বেড়া নির্বাচনী এলাকার সে সময়ের এমএনএ অধ্যাপক আবু সাইদ। আব্বা-আম্মাসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছে থেকে যেদিন বিদায় নিয়েছিলাম সেদিন দুপুরের খাবারটি ছিল খিঁচুড়ী। তার পর দিন আমার আব্বা-আম্মাও অন্য সন্তানদের নিয়ে জলঙ্গি শরণার্থী ক্যাম্পে গিয়ে আশ্রয় নেন। আমার আব্বা খন্দকার রশীদুর রহমান পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের জন্য তৈরি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সেবক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর থেকে আমরা কেউ কারো খবর জানতে পারিনি। তবে আমি যখন ভারতের দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি থানার পানিঘাটা (নকশালবাড়ি) প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে গেরিলা, জেএলসি (জুনিয়র লিডার কোর্স) সহ আর্টিলারি ট্রেনিংরত ছিলাম তখন ওই ট্রেনিং সেন্টারে গেরিলা প্রশিক্ষণ নিতে গিয়েছিলেন আমার প্রতিবেশী নাটোরের আলাইপুর এলাকার বাসিন্দা মোহিত দাসের ছেলে দিলীপ কুমার দাসের সাথে সাক্ষাত হলে তার কাছে জেনেছিলাম আমার আব্বা-আম্মা জলংগির শরণার্থী শিবিরে রয়েছেন। দিলীপও জলঙ্গির সাবরামপুর ক্যাম্প থেকে গেরিলা ট্রেনিংয়ের জন্য পানিঘাটা গিয়েছিলেন। দিলীপের কাছে থেকে শুনেছিলাম আব্বা-আম্মার জীবন কিভাবে কাটছে। আব্বা প্রায়ই মুক্তিযোদ্ধাদের সেই ক্যাম্পে গিয়ে পরিচিতদের সাথে বসে আড্ডা দিতেন। তাদের মধ্যে ছিলেন নাটোরের প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধ খন্দকার আব্দুর রাজ্জাক ও শেখ আলাউদ্দিন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দিলীপ দাস তার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে ভারতে পাড়ি জমান। সেই দিলীপও এখন জীবিত নেই। দীর্ঘ নয় মাস পরিবার ছেড়ে থাকতে খুব কষ্ট হয়েছে। আব্বা-আম্মাসহ পরিবারের প্রিয়ভাজনদের মুখের ছবি ভেসে উঠছিল প্রতিনিয়ত। মন খারাপ হতো প্রায়ই। বিশেষ করে অবসর মুহূর্ত কাটতো প্রিয়জনদের কথা মনে করে। বড় বেশী মনে পড়ত আব্বা-আম্মাসহ আমার বড় ও ছোট বোনের কথা। তবে যুদ্ধের সময় মন থেকে সব কিছু ঝেড়ে ফেলতাম দেশকে স্বাধীন রাষ্ট হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচিত করার প্রবল বাসনা হৃদয়ে ধারণ করে যুদ্ধে অংশ নিতাম। আমরা বিশ্বাস করতাম বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। যুদ্ধে আমরা জয়ী হবোই। মুক্তিযুদ্ধের ৭নং সেক্টরের অধীন ভারতীয় মিত্র বাহিনীর নের্তৃত্বে আমরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। ভারতীয় সেনা সদস্যদের নের্তৃত্বে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গঠন করা হয় তুফানি ব্যাটেলিয়ানের ব্রেভো সেক্টর। প্রশিক্ষণ শেষে ভারতের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় গড়ে তোলা ক্যাম্পে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়। ওই সব ক্যাম্প থেকে রাত্রিতে গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিতে হয়েছে। নওগাঁ, জয়পুরহাট, পাঁচবিবি, হিলিসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ঢুকে গেরিলা যুদ্ধ করতে হয়। এক সময় ভারতের সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিতে হয়।
একাত্তরের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে এবং পরিবরের সকলের উৎসাহে আমি কিশোর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেই। আমি তখন তৎকালীন জিন্নাহ মডেল হাইস্কুলের (বর্তমান সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়) মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি যুদ্ধের মাঠেই ছিলাম। ঢাকায় ২৫ মার্চ কালোরাতের পর নাটোরের সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির নির্দেশে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে পাক সেনাদের প্রতিরোধ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। ২৭ মার্চ নাটোরের তৎকালীন নাটোর টাউন পার্কে (বর্তমানের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ) সর্বদলীয় এক সমাবেশ থেকে ঘোষণা হয় পাকিস্তান বাহিনী প্রতিরোধে। নাটোরে সংগ্রাম কমিটি গঠনের পর চলতে থাকে জঙ্গী মিছিল। বাঙালি যোদ্ধাদের হাতে অস্ত্র বলতে বাঁশের লাঠি, তীর-ধনুক, তরোয়াল, বল্লম আর গাদা বন্দুক। পাকিস্তানিদের ধরে খতম করার তাগিদে অনেকেই ইট হাতে রাজ পথে থেকেছেন। শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ। ওই যুদ্ধের একজন যোদ্ধা হয়ে আমিও তখন থেকেছি নাটোরের রাজপথে। আমার তখন কি বা এমন বয়স হয়েছে। দুরন্তপণার কারণে রাজনৈতিক দলের মিছিল-মিটিংয়ে অংশ নিতাম। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কলেজের তৎকালীন ছাত্রাবাস এবং বর্তমানের রাণী ভবানী মহিলা কলেজ চত্বরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ড্যামি রাইফেল দিয়ে। ইত্যবসরে মুক্তিযোদ্ধারা নাটোরের ট্রেজারির অস্ত্রাগার ভেঙ্গে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এরই মাঝে ৩০ মার্চ নাটোরের লালপুরের প্রত্যন্ত ময়না গ্রামে ঢুকে পড়া একদল পাকিস্তানি সেনাদের সাথে লড়াইয়ে অন্যদের সাথে আমিও যাই সেখানে। যে যুদ্ধ ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ। রাতভর চলা এই যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনারা পরাজিত হয়। এরপর থেকে নাটোরের সর্বত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে। আমার আব্বা ও মায়ের প্রবল ইচ্ছায় আমি প্রতিরোধ কর্মসূচিতে অংশ নিতে থাকি। প্রতিরোধ এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে রাত জেগে পাহারা দিতে হয়েছে। সে সময় আমরা ছিলাম ৭ ভাইবোন। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জণের দিন জন্ম নেয় এক ভাই। স্বাধীনতা পরবর্তী আরো তিন ভাই-বোনের জন্ম হলে আমদের ভাইবোনের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১১ জন। আমার আব্বা খন্দকার রশীদুর রহমান ছিলেন নাটোর সদর হাসপাতালের একজন সিনিয়র নার্স। তার আয়েই চলতো আমাদের টানা পোড়নের সংসার। আমরা সব ভাই-বোন লেখাপড়া করতাম। নানা বাড়ি বগুড়া থেকে অভাবী সংসারের কিছুটা যোগান দেয়া হতো। নানা বাড়ি ছিল বগুড়ায়। সেখান থেকে বড় বোন রওশন আরা জোৎস্নার বিয়ে দেন নানা-নানি। বোনের স্বামী আব্দুর রাজ্জাক তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তনে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বোন রওশন আরা জোৎসনা বগুড়ার মালতিনগর স্টাফ কোয়াটারে থাকতেন শ্বশুর-শ্বাশুরীর সাথে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই পাকসেনারা তাঁর শ্বশুরকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। বোনের শ্বশুর চাকরি করতেন আবগাড়ি (মাদক) বিভাগে। তাঁর স্বামী পাকিস্তান থেকে পালাতে গিয়ে সীমান্তে ধরা পড়েন। এসময় পাকিস্তানী বাহিনীর গুলিতে তিনি নিহত হন। করতোয়া নদীর ধারে ছিল সেই সরকারি স্টাফ কোয়াটার। পাকিস্তানী হায়নার দল আমার বোনের শ্বশুরকে হত্যা করার পর বৃদ্ধা শ্বাশুরী ও শিশু কন্যাকে নিয়ে পালিয়ে জীবন কাটাতে হয়েছে বোনকে। পাকসেনাদের রোষানল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে আমার বোন তার শিশু কন্যাকে নিয়ে সাঁতরে করতোয়া নদী পাড়ি দিয়েছেন।
আমার মা নূর নেসা বেগম ছিলেন সহজ সরল একজন মানুষ। সে সময়ে তাঁর পেটে যে টুকু বিদ্যা ছিল তা দিয়েই তিনি আমাদের পড়িয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রতিরোধের সময় মায়ের নির্দেশে দুপুরে বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসতাম। বাড়ি যাওয়ার পর মা আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতেন। রাতে কোথায় কি পাহারা দিতাম আমার মুখ থেকে শুনতে চাইলে বলতাম। প্রথম প্রতিরোধের সময় পাকসেনাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য শহরের কান্দিভিটা এলাকার রিক্রেয়েশন ক্লাবে স্থাপন করা কন্ট্রোল রুমের কথা বলতাম। পাকসেনাদের নাটোরে আসার সংবাদে গড়ে তোলা হয় প্রতিরোধ। নাটোর শহরের প্রাণ কেন্দ্র তৎকালীন মিনার সিনেমা হলের মোড়ে (বর্তমানের ছায়বাণী সিনেমা হল) তেলের বড় বড় ড্রাম ও বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয় বেরিকেড। এছাড়া শহরের বিভিন্ন প্রবেশ পথেও প্রতিবন্ধক তৈরি করা হয়। মিনার সিনেমা হলের মোড়ের ওই বেরিকেড এলাকার গোপন স্থান জনতা স্টোরের ছাদে। (যেটি এখন নেই) বাঁশের লাঠি ও তীর-ধনুকসহ দেশী অস্ত্র নিয়ে রাত্রিতে পাহারা দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল পাক সেনাদের বাঁধা দিয়ে প্রতিরোধ করা। পাকসেনাদের ভাড়ি অস্ত্রের মুখে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিরোধ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়। প্রথম প্রতিরোধ টিকিয়ে রাখতে না পেরে অর্থাৎ পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের অনেকেই এলাকা ছেড়ে চলে যান প্রতিবেশী দেশ ভারতে। আমিও আমার পরিবারের সাথে ভারতে পাড়ি জমাই। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে এক সময় পাকসেনারা নাটোরে প্রবেশ করে। শুধু প্রবেশই করেনি, স্থাপন করেছিল পাকিস্তানি বাহিনীর ২নং সামরিক হেড কোয়াটার। তারা নাটোরের রাণী ভবানীর রাজবাড়ি, দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি ও তখনকার সিও অফিস যা বর্তমানের উপজেলা পরিষদ অফিস এবং আনসার হল ও পিটিআই স্কুলে অবস্থান নেয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা নাটোরে শক্ত অবস্থান গড়ে তোলে। পাকসেনাদের প্রবল প্রতিরোধের কারণে মুক্তিযোদ্ধারা নাটোরে প্রবেশ করতে পারেনি। সেকারণে আশপাশের জেলাগুলোর বিভিন্ন এলাকায় নাটোরের মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।
১৩ এপ্রিল আব্বা-আম্মাসহ অন্যদের সাথে আমিও ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হই। ঘোড়া গাড়িতে করে সবাই রাজশাহীর সরদা পুলিশ লাইন এলাকায় যাই। পরে সরদা ক্যাডেট কলেজের সামনে থেকে নৌকাতে করে পদ্মা নদী পাড় হয়ে ভারতের দিকে যেতে থাকি। অনেকদূর যাওয়ার পর মাঝি আমাদের নৌকা থেকে নামিয়ে পথ দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এইপথে হেঁটে যেতে হবে। তখনও চারিদিকে পানি থৈ থৈ করছে। আমরা সকলেই ভয় পেয়ে গেলাম। তবে মাঝি আমাদের অভয় দিয়ে বললেন এই পানির মধ্যে হেঁটে যেতে হবে। পদ্মার বুকে চর পড়ার কারণে কোথাও হাঁটু অবধি আবার কোথাও পায়ের গোলাড়ি পর্যন্ত পানি পাবেন। তবে সাবধান করে দিয়ে বললেন দেখিয়ে দেয়া পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে। ভুল করেও দেখিয়ে দেয়া পথের বাম দিকে যাবেন না। এই পথে বড় বড় গর্ত রয়েছে। সেখানে পানির তীব্র স্রোত রয়েছে। সবাই লাইন করে দেখিয়ে দেয়া পানি পথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। পিছনে পাক সেনাদের আসার আতংক নিয়ে দ্রুত পা চালাচ্ছিলাম আমরা। বৃদ্ধরা হাঁটতে পারছিলেন না। তাদের মাঝে মধ্যে কোলে উঠিয়ে নিয়ে হাঁটছিলেন তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যরা। কিছুদূর এগুতেই দেখা হয় ভারতীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের কয়েকজন নারী পুরুষের সাথে। নদীর চরে গজে ওঠা ঘাশ কাটছিল তারা। আমাদের দেখে তারা এগিয়ে এসে জানতে চাইলেন আমরা বাংলাদেশী শরণার্থী কিনা। কোথায় যাব জানতে চেয়ে ওদের দু’জন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। ওদের আতিথিয়তায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। এক সময় আমরা নদী পথ ছেড়ে মেঠো পথে হাঁটা ধরলাম। একসময় ভারতের মাটিতে পা দিলাম। ভারতের ধনিরামপুর গ্রামের এক গৃহস্থের বাড়িতে উঠে কিছু সময় অতিবাহিত করি। তারা খিঁচুড়ী রান্না করে আমাদের সকলের খাবার ব্যবস্থা করেন। ২২ সদস্যের কাফেলা ছিল আমাদের। প্রত্যেকেই পেট ভরে খেয়ে গৃহস্থের পরিবারের সদস্যদের সাথে কুশল বিনিময় করে রওনা বহরমপুরের বাস ধরতে। বাহরমপুরগামী বাস ওঠার পর দেখা হয়, নাটোরের মুক্তিযুদ্ধ সংগঠকদের কয়েকজনকে। যারা ওই বাসের যাত্রী ছিলেন। ওই বাসের যাত্রী ছিলেন প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা মজিবুর রহমান সেন্টু, বীর মুক্তিযোদ্ধা কামরুল ইসলাম ও অনাদি বসাক। কুশল বিনিময় করে একই বাসে মুর্শিদাবাদ জেলা সদর বাহরমপুর গেলাম। সেখানে আমরা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেই। এসময় শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থী খোঁজ খবর নিতে এসে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক নাটোরের এমসিএ শংকর গোবিন্দ চৌধুরীর সাথে আমাদের দেখা হয়। আমার একে অপরের প্রতিবেশী হওয়ায় তিনি আমার আব্বাকে পছন্দ করতেন। শংকর কাকা আব্বার সাথে কথা বলতে বলতে অন্য দিকে গেলেন। যাওয়ার সময় আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কোন কিছুর প্রয়োজন হলে তার সাথে যেন দেখা করি। এর একদিন পর আমি আমার পরিবারের মোহ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা হই। পরে পাবনার এমএনএ অধ্যাপক আবু সাইদের গড়া বালুরঘাটের কুড়মাইল ও মালঞ্চ ক্যাম্প হয়ে গেরিলাসহ উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিতে নকশালবাড়ির পানিঘাটা ক্যাম্পে যাই। সেখানে প্রশিক্ষণ শেষে আমাদের রায়গঞ্জ ক্যান্টনমেন্ট হয়ে প্রতিরামপুর ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে সেখান থেকে আবারও পশ্চিম দিনাজপুরের অযোদ্ধা সীমান্ত এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। অযোদ্ধার ক্যাম্পে বাংকারে থাকতে হয়েছে আমাদের। রাতে বের হয়ে ভারতীয় সেনাকর্মকর্তার নের্তৃত্বে বাংলাদেশে প্রবেশ করে যুদ্ধ করতাম পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে। দুই একদিন রাজাকারদের সাথেও যুদ্ধ করতে হয়েছে। তবে রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি টের পেয়েই পিছু হটে দ্রুত পালিয়ে যেত। এভাবেই প্রায় প্রতি রাতেই বাংলাদেশের মধ্যে ঢুকে গেরিলা যুদ্ধ অংশ নিতাম এবং ভোর হওয়ার আগেই ক্যাম্পে ফিরে আসতাম। একসময় ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পর ভারতীয় মিত্র বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নেই। আমরাও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেই। সম্মুখ যুদ্ধের সময় আমাদেরকে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর পোষাক সরবরাহ করা হয়। আমরা হিলি হয়ে এবং পাঁচবিবি সীমান্ত দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে বাংলাদেশের ভিতরে প্রবেশ করি। ১২ ডিসেম্বর রংপুরের গোবিন্দগঞ্জ শত্রু মুক্ত হওয়ার পর বগুড়ার দিকে অগ্রসর হই। ১৩ ডিসেম্বর বগুড়া মুক্ত হয়। ১৬ ডিসেম্বর সারাদেশ শত্রু মুক্ত হওয়ার খবরে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ি। নাটোরে আসার জন্য ছটফট করতে থাকি। মনেপড়ে আববা-আম্মা ও পরিবারের সদস্যসহ সহপাঠি বন্ধুদের কথা। আমাদের অস্ত্র জমা নেয়ার পর ১৭ ডিসেম্বর নাটোরের পথে রওনা হই। এসময় বিধ্বস্ত বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় কিছু পথ হেঁটে এবং কিছু পথ ট্রেনে নাটোরে আসি। নাটোরে আসার সময়ও আমার পরনে ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর পোষাক। প্রিয়জন ও বন্ধু বান্ধবদের দেখার প্রবল ইচ্ছায় সবকিছু ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু ১৭ ডিসেম্বর ট্রেনে নাটোর এসে নামার পর আঁতকে উঠতে হয়েছে আমাকে। তখনও নাটোর শহরের সর্বত্র পাকসেনারা অবস্থান করছিল। লোকমুখে পরিস্থিতি মিত্রবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে জেনে হাঁটতে শুরু করলাম প্রিয় বন্ধু উত্তর বড়গাছা হাফরাস্তা এলাকার সুজাউল হামিদের বাড়ির উদ্দেশ্যে। টালির ছাউনি ও মাটির দেওয়ালের ছোট্ট একটি ঘরে বসে সুজা তার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিমায় গজল গান করা নিয়ে মত্ত ছিল। পিছন থেকে তার নাম ধরে ডাকতেই তার ঘরে পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্য ভেবে সে আঁতকে ওঠে। পরক্ষণেই চিনতে পেরে আবেগে আমাকে সে জড়িয়ে ধরে। দীর্ঘ নয়মাস পর দুই বন্ধুর দেখা হওয়া দু’জনেই আবেগআপ্লুত হয়ে পড়ি। স্বাভাবিক হওয়ার পর ওর কাছে থেকেই সবার খোঁজ খবর নিয়ে বেরিয়ে পড়ি অন্যদের সাথে দেখা করতে। দীর্ঘদিন পর সবার সঙ্গে দেখা হবে সে এক অন্যরকমের অনুভূতি। আমার পরিবারের সবাই তখনও ভারতে অবস্থান করায় বন্ধু হীরার বাড়িতে রাত্রি যাপন করি। ২১ ডিসেম্বর নাটোরে অবস্থানরত পাকসেনাদের আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের পর পুনরায় বগুড়ার পুলিশ লাইনে আমাদের ক্যাম্পে ফিরে যাই। সেখানে আমাদের আনুষ্ঠানিক বিদায় জানানোর পর আমি আবারও নাটোরে ফিরে আসি।
৭১এর ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সাথে বগুড়া অঞ্চলে যুদ্ধরত অবস্থায় আমার বড় বোন যে গ্রামে অবস্থান করছিলেন সেই গ্রামের মেঠো পথ ধরে আমরা বগুড়া শহরের দিকে যাচ্ছিলাম। এসময় এক নারী কন্ঠ আমার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকাডাকি করছিলেন। আমি খেয়াল করিনি। কিন্ত আমার সহযোদ্ধা চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলার আলীনগর গ্রামের মহসীন আলী বুলু তা দেখে আমাকে বললে আমি গুরুত্ব দেইনি। বগুড়া শত্রুমুক্ত হওয়ার পর বুলুর চাপাচাপিতে আমরা ক’জন সেই গ্রমে যাই। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল গ্রামে প্রবেশের খবর পেয়ে অনেকেই ছুটে আসেন আমাদের দেখতে। আমাকে দেখেই আমার বড় বোন আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। আমিও নিজেকে সম্বরণ করতে পারিনি। দুই ভাইবোনের এই মিলনে অনেকেই আনন্দে কেঁদে ফেলেন। এসময় এলাকায় এক অভূতপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে দেশ স্বাধীনের পর কন্যা সন্তানসহ আমার বোনকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসি। স্বাধীনতার পর থেকে আমরা সব ভাইবোন বড় বোনের আদর সোহাগ ও ভালবাসায় ৫১ বছর এক সঙ্গে কাটিয়েছি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৭২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নাটোর সফরে আসেন। বড় বোন রওশন আরা জোৎস্না উত্তরা গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি বোনকে বলেন, জোৎস্না তুমি আমার মেয়ের মত। তোমার জন্য আমি রয়েছি। তোমার স্বামী যদি পাকিস্তানে বেঁচে থাকেন তাহলে তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনব। একথা বলে বঙ্গবন্ধু আমার বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সেই আদরমাখা হাতের ছোঁয়া পেয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখছিলেন আমার বোন। কিন্তু ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করায় বোনের সেই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। আমাদের টানাপোড়নের সংসারে নিজের খরচের জন্য সেলাই মেসিনে কাপড় সেলাইসহ হাতের কাজ করতেন। আমাদের কারো কোন বাধা নিষেধ মানতেন না। প্রিয়জন কাউকে কাছে পেলে ৭১ স্মৃতিময় দিনগুলোর গল্প করতেন আমার বোন। ২০২০ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পাকসেনা ও তাদের দোসর রাজাকার আলবদরদের নির্মমতা ও নৃশংসতাকে ভুলতে পারছিলেন না আমার বোন। তবে শান্তনা খুঁজেছেন মুক্তিযুদ্ধের বিজয় এবং রাজাকার ও স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচার হওয়াতে। বগুড়া অঞ্চলে যুদ্ধ শেষে পুনরায় ফিরে আসি নাটোরে।
ফিরে আসার পথে মনের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে অনেক কাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের নিয়ে তুফানিয়া ব্যাটেলিয়ান নামে একটি ব্যাটেলিয়ান গঠন করা হয়। ৭নং সেক্টরের অধীন ভারতীয় মিত্র বাহিনীর নেতৃত্বে গড়ে তোলা এই ব্যাটেলিয়ানের সদস্য হয়ে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সাথে একসাথে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি। মুক্তিযুদ্ধের শেষভাগে বগুড়া অঞ্চলে যুদ্ধরত অবস্থায় বিজয় অর্জিত হয়। মুক্তিযোদ্ধাসহ মুক্তিকামী বাঙালিরা বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠেন। ভারতীয় মিত্র বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাঁড়াশি আক্রমনের কারণে ১৩ ডিসেম্বর বগুড়া পাকহানাদার মুক্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জিত হওয়ায় নিজেকে গর্বিত মনে হতে থাকে। স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে শিশু ও শৈশব কালের অনেক স্মৃতিময় কথা। মনে পড়ে নাটোরের সহপাঠি প্রিয় বন্ধুদের মুখ। প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গত হয়েছেন তাজুল ইসলাম তাজু, আব্দুল ওহাব, খসরু চৌধুরী, আমিনুল হক, দেলোয়ার হোসেন বাচ্চু, রুহুল আবেদীন হীরা, খাইরুল ইসলাম, রুহুল আমিন ও বাবুয়া বসাক। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জনের পর এসব বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের জন্য মন উতলা হয়ে ওঠে। জীবিত বন্ধুদের মধ্যে এখনও কুশল বিনিময় হয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শহিদুল ইসলাম বাচ্চু, সাবেক ফুটবলার আল মামুন, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সুজাউল হামিদ, শিক্ষানুরাগী প্রফেসর মুজিবুল হক নবী, প্রফেসর অলোক মৈত্র। ভারতবাসী হয়েছেন বসুদাম কুণ্ড, সুবল কুমার দাস, দিলীপ কুমার আগরওয়ালা। ১৬ ডিসেম্বর সারা দেশ বিজয় অর্জিত হলেও চারদিন পর অর্থাৎ ২১ ডিসেম্বর নাটোর শত্রমুক্ত হয়। এদিন নাটোরের মানুষদের আনন্দ উৎসব ছিল বাঁধভাঙ্গা। ২০ ডিসেম্বর রাত থেকেই উত্তরা গণভবন এলাকায় জয়বাংলা ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। যুদ্ধ শেষে একটি স্বাধীন দেশের মুক্ত বাতাসের ঘ্রাণ নিতে শত শত নারী পুরুষ বাড়ির বাহিরে বের হয়ে আসেন। পরিবারের সাথে এই আনন্দ উদ্যাপন করতে আমাকে আরও প্রায় একমাস অপেক্ষা করতে হয়েছে। ভারতে অবস্থান করা আব্বা-আম্মাসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের বাংলাদেশে আসার অপেক্ষার প্রহর এক সময় শেষ হয়। জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় তারা ফিরে আসলে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার যন্ত্রণাও শেষ হয় আমার।