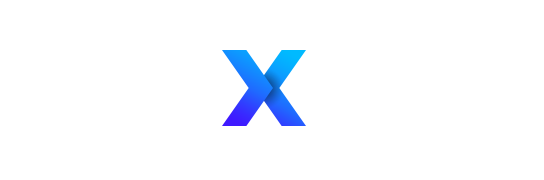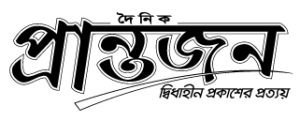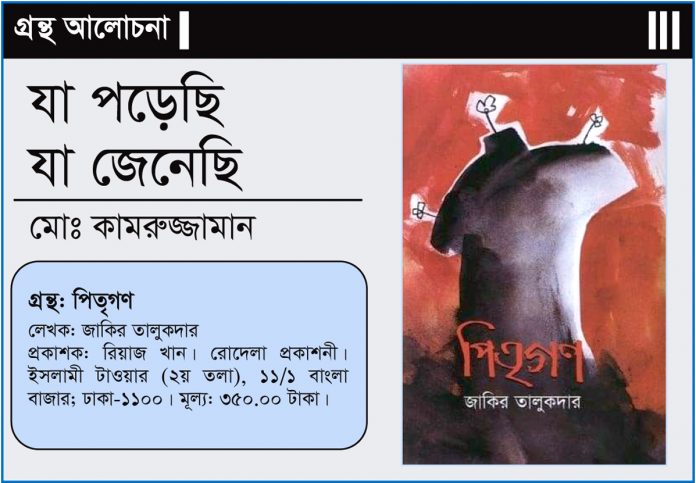পিতৃগণ
লেখক: জাকির তালুকদার
প্রকাশক: রিয়াজ খান। রোদেলা প্রকাশনী। ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), ১১/১ বাংলা বাজার; ঢাকা-১১০০। মূল্য: ৩৫০.০০ টাকা।
প্রথম পর্ব
পিতৃগণ উপন্যাসের দুটো পর্ব। এটি ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাস। এর প্রতিটি বাক্যে তথ্য-উপাত্ত, কৌতূহল উদ্দীপক ও লোমহর্ষক বর্ণনায় সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম পর্বে মহীপালের বিরুদ্ধে কৈবর্তদের যুদ্ধে জয় এবং ওদের সুখে-শান্তিতে বসবাসের কথা বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে কৈবর্তদের উদারতা ও অপরের প্রতি বিশ্বাস এবং যুদ্ধে রামপালের চুক্তিভঙ্গ ও শঠতার কারণে ওদের পরাজয় ও নিশ্চিহ্ন হওয়ার বিষয়টি উপজীব্য হিসেবে নেওয়া হয়েছে।
বরেন্দ্রীর অপর নাম কট্টলি। সেখানে কৈবর্তদের একটি গ্রাম দেদ্দাপুর। কৈবর্তদের কেউ মানুষ বলে গণ্য করে না। ওরা অসুরযোনী থেকে জন্মেছে বলে রাজবংশীয় ও ব্রাহ্মণগণ মনে করে। এই ভূমিপুত্রদের সবাই অস্পৃশ্য ভূমিদাস ভাবে। ব্রাহ্মণগণ ওদের মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে কেঁচোর মতো চাষবাসের উপযুক্ত প্রাণি মনে করে। তারা মনে করে কৈবর্তরা যতদিন ওদের আরাধ্য ও পূজনীয়দের ছেড়ে আর্য দেবতার শরণ না নিবে ততদিন তাদের কোন অধিকার দেওয়া যাবে না। তারা শুধু শাসিত হবে, শাসক হবে না।
কৈবর্তরা দেবভাষা (সংস্কৃত) বুঝে না। ওদের এই ভাষা শেখায় শাস্ত্রে বারণ আছে। ওদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা নেই। ওরা তিন বেলা পেটপুরে খেতে পাওয়ার ভাগ্য নিয়ে জন্মায় না। কিন্তু শত কষ্ট সহ্য করেও ওরা রাজ-পুরুষের সমুখে অশ্রু ফেলে না। ওরা কারও কাছে হাত পাততে জানে না। এরা কারও কাছে পরাজয় মানে না। মানুষ মুখ দিয়ে খায়, মাকে মা ডাকে, সন্তানকে আদর করে। সুতরাং ওদের কাছে ভূষাকালির ছাপের চেয়ে মুখের কথার মূল্য অনেক বেশি।
কৈবর্ত কি! কৈবর্ত ওলান ঠাকুরের তৈরি মাটি। কৈবর্তরা নিজদের ভূমিপুত্র গণ্য করে। কৈবর্তরা এক কথার মানুষ। ওরা প্রাণের বিনিময়ে কথা রক্ষা করে। ওরা শান্তিপ্রিয় ও স্বাধীনচেতা মানুষ। ওরা পরের বিষয়ে নাক গলায় না। কিন্তু অপরে তাদের বিষয়ে নাক গলাবে এটাও সহ্য করে না। ওরা জন্মগত ভাবেই কঠোর পরিশ্রমী ও কর্মঠ। এরা মাটিকে চিনে নিঃশ্বাসের মতো। মাটিই ওদের মা। ওরা মাটির সঙ্গে দিবানিশি কথা বলে। ওদের স্পর্শে ঊষর মাটিতে সোনা ফলে। সুতরাং ওদের ভূমিদাস হিসেবে পাওয়ার জন্য সবাই নানান বাহানায় কিনে নেয়। ওরা যাযাবর জাতি নয়। ওলান ঠাকুর ওদের হাট-ঘাট-মাঠ-বন-খাল-নদী সব দিয়েছে।
ওদের পূজ্য দেবতার নাম ওলান ঠাকুর। প্রতিটি কৈবর্ত গাঁয়ের মুখে একটি লম্বা ও একটি চেপ্টা পাথর দাঁড় করানো আছে। ওরা গাঁওদেবতা ও গাঁওদেবী। ওরা গাঁয়ের মানুষের রক্ষাকর্তা। কৈবর্তরা নিজেরাই তাদের অমাত্য নির্বাচন করে সেই অমাত্যের নির্দেশ পালন করে। কিন্তু রাজপুরুষরা ওদের সুখ সইতে পারে না। প্রায়শঃই অত্যাচার করে। কৈবর্ত যুবকদের বিষ্টির (বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম প্রদান) জন্য বাধ্য করে। জমির ফসলে করারোপ করে। বনে শিকার করতে দেয় না। জলাধারে মাছ ধরতে দেয় না। ওদের নারীদের প্রতি লোলুপ হাত বাড়ায়। তখন ওদের সঙ্গে অসম যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু পাল সম্রাটের জগৎজয়ী সেনারাও কৈবর্তদের সঙ্গে যুদ্ধে হার মেনেছে। তাদের সৈন্য ও সেনাপতিরা এদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে নাকানি-চুবানি খেয়ে বিষ্মিত হয়েছে।
দেদ্দাপুরের এক কৈবর্ত বট্যপ। তার স্ত্রী বিবানি। তার প্রসব ব্যথা শুরু হয়। তিন দিন পেরিয়ে যায়। তার সন্তান জগতের আলোর মুখ দেখার জন্য পেটের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে না। কেউ কোন উপায় করতে পারে না। ওলান ঠাকুরের চরণ ধোয়া জলেও কাজ হয় না। বিবানীর প্রসব-যন্ত্রণা সইতে না পেরে বট্যপ দেবগ্রাম থেকে ধাত্রী বিল্ববালাকে ডেকে আনে। সে আসার পরপরই বিবানির জঠর থেকে পপীপের জন্ম হয়। কিন্তু বিল্ববালার সঙ্গে চুক্তির দশ দ্রুম ও ঊনিশ কার্ষাপণ সে পরিশোধ করতে পারে না। তখন সদ্যজাত পপীপ ও স্ত্রী বিবানিকে আঁতুড়ঘরে রেখে বট্যপ আত্মবিক্রিত হয়ে বিল্ববালার পারিশ্রমিক পরিশোধ করে কামরূপে ভূ-স্বামী রামশর্মার ইক্ষু ক্ষেতে কাজের জন্য চলে যায়।
পপীপ সাত বছরের শিশু। এক ভোরে দেদ্দাপুরে রাজ-পুরুষদের ঢ্যাঁড়ার শব্দে কৈবর্তদের ঘুম ভাঙ্গে। তারা এই ঢ্যাঁড়ার শব্দকে অনিবার্য ক্ষতি ও ধ্বংসের সংকেত বলে মনে করে। তারা পড়িমরি করে ছুটে আসে। তখন তারা খবর পায় আত্মবিক্রিত বট্যপ আশানুরূপ শ্রম দিতে পারছে না এবং তার ঋণ পরিশোধ হচ্ছে না। সুতরাং তার ছেলেকেও রামশর্মার ইক্ষু ক্ষেতে কাজ করে দেনা পরিশোধ করতে হবে। সেই সাত সকালে দেদ্দাপুরে এক হাহাকার রব উঠে। রাজ-পুরুষরা বিবানির সকল বাধা উপেক্ষা করে পপীপকে নিয়ে কামরূপের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।
কামরূপের পথে পপীপ আরও আত্মবিক্রিত কৈবর্তদের দেখা পায়। তারাও ঋণ পরিশোধের জন্য অথবা পারিবারের অন্য সদস্যদের সুখের আশায় ঋণের টাকা নিয়ে আত্মবিক্রিত হয়ে ত্রিস্রোতা নদী পেরিয়ে কামরূপে শ্রম দিতে চলে যায়। এই নদী পার হওয়া মানে কৈবর্ত জীবন থেকে বিদায় নেওয়ার সমতুল্য। পপীপ রাজপুরুষদের সঙ্গে নৌকায় উঠে ত্রিস্রোতা নদী পেরিয়ে কামরূপে রামশর্মার ইক্ষু ক্ষেতের ক্রীতদাস তার জন্মদাতা বট্যপের দেখা পায়।
কামরূপের রাজা মহীপাল। পাল সাম্রাজ্যের এগারটি সামন্ত রাজ্য রয়েছে। মহীপাল রাজা হলেও মহাঅমাত্য ভট্টবামনের আঁকা ছকে পুরো রাজ্য চলে। তার পরামর্শে পররাষ্ট্র ও অন্তঃরাষ্ট্র শান্তি প্রতিষ্ঠা মন্ত্রী পদ্মনাভ। তিনি একজন সজ্জন ও অপরের রাষ্ট্রের লোকজনের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। প্রধান সেনাপতি কীর্তিবর্মা। তার বিশাল দেহের মতোই তার বুদ্ধিও মোটা। তার কাছে ভট্টবামনের কথাই শিরোধার্য। সে শত্রু ও বন্দীদের প্রতি এমন অত্যাচার করতে পারে যা দেখে যে কোন সংবেদনশীল মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে। রাজ্য পরিচালনায় এই প্রধান চার ব্যক্তির মধ্যে ভট্টবামনের কাছে বরেন্দ্রী ও কৈবর্তরা মূল সমস্যা।
পাল সম্রাজ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধদের পাশাপাশি কোল, ভীল, শবর, পুলিন্দ, কৈবর্ত, কোচ, রাজবংশী, মেচ, হাড়ি এবং আরও বিচিত্র জাতি ও ধর্মের মানুষ বাস করে। আর আর্যরা এদের উপর আধিপত্য চালানোর জন্যই এখানে এসেছে। তারা মনে করে অন্য জাতি ও ধর্মের মানুষ আর্য ও ক্ষত্রিয়দের সেবা করা সুযোগ পেয়ে নিজকে ধন্য মানছে।
বরেন্দ্রীর প্রাদেশিক প্রধান অমাত্য একজন কৈবর্ত। সে দিব্যোক। সে আগের সকল কৈবর্ত অমাত্যদের চেয়ে বুদ্ধিমান। ভট্টবামন দিব্যোককে প্রচণ্ড ঘৃণা করে। সে অন্য কৈবর্তদের মতো নয়। তাকে স্বর্ণমুদ্রা, মদ ও নারী দিয়ে কেনা যায় না। সে স্বজাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে আর্যদের সেবাদাসে পরিণত হয় না। সে অমাত্য নির্বাচিত হওয়ার পর বরেন্দ্রীতে দাদন ব্যবসা কমেছে। ওদের আত্মবিক্রয়ের সংখ্যাও কমেছে। কৈবর্তরা আগের তুলনায় অনেক সুখে আছে। আর্যরা কৈবর্তদের ধর্মীয় প্রভাবে ও অর্থনৈতিক চাপে পদদলিত রাখতে চায়।
আর্যরা যেমন চণ্ডাল বা কৈবর্তদের তাদের দেবভাষা শিখতে দেয় না, তাদের পূজা-অর্চনায় যোগদান করতে দেয় না ঠিক তেমনই তারা বৌদ্ধদের সংঘে যেন যেতে না পারে সে বিষয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু সেই কৈবর্তরাই তাদের অসুরযোনীতে জন্মের প্রায়শ্চিত্য স্বরূপ বৌদ্ধদের মহাবিহারের ব্যয়-নির্বাহ করতে বাধ্য থাকে। মহাবিহারের ভিক্ষু প্রধানদের ভট্টবামন এসব পরামর্শ দেওয়ার সময় কৈবর্তদের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে ঘৃণায় বার-বার ভ্রু-কুঞ্চিত করে।
কামরূপে রামশর্মার দিগন্ত বিস্তৃত ইক্ষু ক্ষেতে অনেক কৈবর্ত কাজ করে। তারা সবাই আত্মবিক্রিত ক্রীতদাস। এই ইক্ষু চাষ অত্যন্ত লাভজনক। আখ ছাড়া গুড় হয় না। গুড় ছাড়া মিষ্টান্ন হয় না। মিষ্টান্ন ছাড়া হিন্দুদের পূজা হয় না। তাছাড়া আখ থেকে সোমরস তৈরি হয়। এই সোমরস ছাড়া আর্য হিন্দুদের কোন বিনোদন হয় না। সুতরাং আখচাষের জন্য ভূমি মালিকদের ঝোঁক বেশি।
বট্যপের সঙ্গে পুত্র পপীপের পরিচয়ের পর পপীপকে রামশর্মার সবজি বাগানে জল-সিঞ্চনের কাজে নিয়োগ দেওয়া হয়। সেখানে গোলগোমীরা (যারা ঘর পরিষ্কারের দায়িত্বপালন করে) তারা পপীপকে স্নেহ করে। সেখানে মল্ল’র সঙ্গে পপীপের পরিচয় হয়। মল্ল একজন বিশালদেহী তাগড়া জুয়ান কৈবর্ত। তার দেহে অসুরের শক্তি। সে শিকল-পরা বিকল বরেন্দ্রীকে সইতে পারে না।
মল্ল রামশর্মার এক ডাকাবুকো ক্রীতদাস। সে রামশর্মাকে বাঘের থাবা থেকে প্রাণে বাঁচিয়েছিল। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে রামশর্মা পরিবারের সদস্যদের দেখা-শোনার জন্য নিয়ে যায়। রামশর্মার কন্যা মুকুলিকার সঙ্গে তার প্রেম হয়। তার কাছে মল্ল অক্ষরজ্ঞান লাভ করে। কিন্তু শুদ্রের বীর্যে মুকুলিকা গর্ভবতী হলে এটা কেউ মানতে পারে না। কারণ এটা আর্যজাতির কলঙ্কচিহ্ন। তাই গর্ভস্থ সন্তানসহ মুকুলিকাকে পুড়িয়ে মারা হয়। এরপর মল্ল মুক্ত স্বাধীনভাবে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। সে পপীপকে বিদ্যা শেখাতে চায়। যে বিদ্যাহীনতা তাদের পশ্চাদপদতার মূল কারণ।
ঊর্ণাবতী একজন দেবদাসী। সে উর্বশীতুল্য অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী। সে অন্যান্য দেবদাসীদের মতোই পুরোহিত, সেবায়েত ও অভিজাতদের ভোগ্য। কিন্তু সে এই নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চায়। সে মুক্তি পায় না। সে আপন মনে ভাবে, নিজের শরীরের মাংসই হরিণীর মৃত্যু ডেকে আনে। আর ঊর্ণাবতী তোমার রূপই তোমার সর্বনাশ ডেকে এনেছে।
একদা মল্ল ঊর্ণাবতীকে পাঁচজন পুরুষের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। এরপর ঊর্ণাবতী মল্লকে তার পূজনীয় দেবতার আসনে বসায়। মল্ল তার কাছে এলে সে নিজ হাতে তার পা ধুইয়ে মাথার চুলে মুছে দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করে। ঊর্ণাবতী লেখা-পড়া জানে। সে মল্ল’র অনুরোধে পপীপকে শাস্ত্রজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব নেয়। কিন্তু রামশর্মার কাছ থেকে পপীপকে মুক্ত করবে কিভাবে! তাই সে রামশর্মার প্রাসাদে যায়। সে তার দেহদানের বিনিময়ে পপীপকে কিনে নেয়।
কৈবর্ত যুবক-যুবতীদের ক্ষেত্রপূজা চলে। কিন্তু এ পূজায় রাজ-পুরুষরা বাধা দেয়। কারণ এই গ্রামে এমন অশ্লীল ও অশাস্ত্রীয় পূজা চলতে পারে না। কৈবর্তরা এটা মানে না। তারা দিব্যোকের শরণাপন্ন হয়। দিব্যোক এমন একজন প্রকৃত নেতা যে কখনও নিজের ক্রোধ, উচ্ছ্বাস, ভীতি, আবেগ কারও সমুখে প্রকাশ করে না। কৈবর্তরা বিদ্রোহ করতে চায়। ওরা ওদের কট্টলি মাকে ওদের মতো করে পেতে চায়। তাদের বিদ্রোহের আশংকায় ভট্টবামন কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। কৈবর্তরা শান্ত হলে সেই রাতেই তাদের ঝুপড়ি ঘরগুলোতে অগ্নি সংযোগ করা হয়।
যারা কৈবর্তদের অত্যাচার করেছে দিব্যোক তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে চায়। তবে তারা সাধারণ হিন্দু ও বৌদ্ধদের উপর আক্রমণ করতে নারাজ। তাছাড়া তারা নারী ও শিশুদেরও আক্রমণ করবে না। দিব্যোকের একজন বিশ্বস্ত লোক উগ্র। নাম উগ্র হলেও সে খুব ধীর ও স্থির চিন্তার মানুষ। তাই প্রত্যাঘাত-পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব এই উগ্র’র কাঁধে দিব্যোক অর্পণ করে। আর্যদের জন্য আরেক ত্রাস কৈবর্তের নাম ভল্ল। তাকে আক্রমণ অভিযানের সম্মুখ ভাগে রাখা হয়। যারা ক্ষেত্রপূজার রাতে কৈবর্তদের অত্যাচার করেছে তাদের ধরে এনে শাস্তি দেওয়া হয় এবং লাঞ্ছিত করা হয়।
ভট্টবামনের কাছে বরেন্দ্রী সবচেয়ে স্পর্শকাতর। তাই এখানে খোলদের (গোয়েন্দা) জন্য বিশেষ বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তবু যেন সঠিক সময়ে সঠিক খবরগুলো ভট্টবামনের কাছে পৌঁছে। রাজপুরুষদের লাঞ্ছনার খবর পেয়ে ভট্টবামন কীর্তিবর্মার নেত্রীত্বে পাল সৈন্যদের পাঠিয়ে বরেন্দ্রীতে সকল কৈবর্তকে হত্যার পরিকল্পনা করে। তারা মহীপালের স্বাক্ষরিত চিঠি পাঠিয়ে দিব্যোককে রাজধানীতে ডেকে পাঠালেও এটা মূলত ভট্টবামন ও কীর্তিবর্মার কারসাজি। কারণ তারা জানে কোন না কোনভাবে দিব্যোককে দুনিয়া থেকে বিদায় করতে পারলে কৈবর্তদের মুক্তি আরও একশত বছর পিছিয়ে যাবে।
মহারাজ মহীপালের প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পরপরই এক পাত্র পানা (শরবত) পানের অভ্যাস। এসব পানা ঋতুভিত্তিক বিভিন্ন ফলাদি থেকে তৈরি। কিন্তু এক প্রত্যুষে সব উলট-পালট হয়ে যায়। সেই প্রত্যুষে মহারাজের বিশ্বস্ত খোল (গুপ্তচর) খবর আনে যে দাক্ষিণাত্যের শক্তিমান রাজা রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাতীর কুক্ষিগত করার জন্য চতুরঙ্গ সৈন্যদল নিয়ে পাল সাম্রাজ্যের দিকে ধেয়ে আসছে। পদ্মনাভ শান্তি চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ এড়াতে চাইলেও কীর্তিবর্মা ও ভট্টবামন এটাকে দুর্বলতা ভেবে মহীপালকে যুদ্ধে উসকে দেয়। ফলে তারা যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হয়।
ওদিকে ভট্টবামনের কূট-কৌশল বুঝতে না পেরে দিব্যোক তার স্বজাতি হাজারও কৈবর্ত যুবকদের নিয়ে রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তারা কট্টলি বা বরেন্দ্রীকে ফিরিয়ে আনা অথবা ওলান ঠাকুরের নামে মরার শপথ গ্রহণ করে। দিব্যোক রাজধানীর উত্তরে উগ্রকে, দক্ষিণে রুদোককে, পশ্চিমে তার বাল্যবন্ধু বুধিয়াকে এবং দিনুয়াকে পশ্চিম দিকে পাঠায়। পরিকল্পনা মতো তারা রাজধানীতে পৌঁছে নগরীর চার সিংহ দুয়ারের অবস্থান নেয়। তারপর মহারাজের অনুমতি পেলে দিব্যোকসহ পাঁচজন গিয়ে মহারাজকে অবহিত করবে যে রাজপুরুষরা, হিন্দু পুরোহিতরা ও বৌদ্ধ মঠাধ্যক্ষরা কিভাবে কৈবর্ত ও অন্যান্য ভূমিপুত্রদের অত্যাচার-নিপীড়ন চালাচ্ছে।
দিব্যোক একজন প্রাদেশিক অমাত্য। তার রাজকীয় মর্যাদা আছে। কিন্তু যখন দিব্যোকসহ পাঁচজন সিংহ দুয়ারের দিকে এগিয়ে গেলো তখন দুয়ার বন্ধ করে দেওয়া হলো। এবং সমবেত কৈবর্তদের উপর সহসা শত শত তীর ছুঁড়তে লাগলো। কয়েকজন কৈবর্ত মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যেই দিব্যোক কৈবর্তদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। মল্ল, রুদোক, উগ্র ও পরভুর নেতৃত্বে কৈবর্তযোদ্ধারা পাল সেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মহারাজের পুরো সেনাদল গঙ্গাতীরে রাজেন্দ্র চোলের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। সুতরাং কৈবর্তদের সামনে রাজধানীর মাত্র কয়েক শত সৈন্য বেশিক্ষণ টিকতে পারে না।
কৈবর্তরা দ্বাররক্ষকদের হত্যা করে নগরীর সিংহ দুয়ার খুলে দেয়। তারা পানির স্রোতের মতো নগরীতে প্রবেশ করে। তাদের কেউ রুখতে পারে না। শত শত বৎসরের নিপীড়ন-লাঞ্ছনা-শোষণ-অমানবিক আচরণের শিকার এইসব কৈবর্তদের বুকে স্বর্বস্ব হারানোর যন্ত্রণা-অপমান যে প্রচণ্ড ঘৃণা হয়ে জমেছিল আজ তা উম্মুক্ত করার পথ পায়। গৌড়ের সেনাদল কচুকাটা হয়। ওদের লুণ্ঠনে বাধা দিতে গিয়ে অনেক নগরবাসী প্রাণ হারায়। রাজপ্রাসাদ বিধ্বস্ত হয়। অনেকে পালিয়ে যায়। একজনের বল্লম মহারাজ মহীপালের বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়।
কৈবর্তরা বিধ্বস্ত নগরের নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে তুলে নেয়। তারা বরেন্দ্রীর সঙ্গে পুণ্ড্ররাজ্যও ফিরে পায়। তারা ভাবে তাদের দেবতা ওলান ঠাকুর দিব্যোকের বেশে জন্ম নিয়ে তাদেরকে শত শত বছরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছে। তারা দিব্যোকের নামে জয়ধ্বনি দেয়।
দ্বিতীয় পর্ব
ছল-চাতুরি-মিথ্যাভাষণ-ব্যভিচার আর্যদের মজ্জাগত। আর্যরা কখনও গঙ্গার এপারে যুদ্ধ করতে সাহস পায়নি। যতবার যুদ্ধ করতে এসেছে ততবার পালিয়েছে। পরে তারা মনে লোভ ও অসীম পাপ লুকিয়ে রেখে হাতে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে আশ্রয়ের প্রত্যাশায় বরেন্দ্রী ও পুণ্ড্রতে এসেছে। ওরা মাটিকে পূজা করতে জানতো না। ভূমিপুত্ররা ওদের বুকে টেনে নেওয়ার সুযোগে ওরা মারণাস্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে ওদের উপর হামলে পড়ে ওদের রাজা বাসুদেবকে হত্যা করে বরেন্দ্রী দখল করে নেয়। তারপর সেখানে মনুর বিধান চালু করে। যেখানে বলা হয়েছে এই ভূমিপুত্ররা নীচ জাতি। এখানে রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক নায়ক-খলনায়ক, সুর-অসুরের চরিত্র আলোচনা করা হয়েছে।
বরেন্দ্রীর ভূমিপুত্ররা দিব্যোকের নেতৃত্বে বুকের রক্ত ঢেলে শত বছরের সংগ্রামের পর ওদের মাটিকে মুক্ত করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন বিজয় এই প্রথম। পাল-রাজাদের পরাজয়ের পর মল্ল চর পাঠিয়ে ঊর্ণাবতীকে তার বাঞ্ছিত কোন পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যেতে বলে। কিন্তু সে মল্লকেই তার বাঞ্ছিত পুরুষ হিসেবে বেছে নেয়। উদারতা এই ভূমিপুত্রদের অন্যতম দুর্বলতা। সেই সুযোগ নিয়ে রক্ষীদের যোগসাজসে রামপাল রাজকোষের সমস্ত অর্থ ও ধন-রত্ন নিয়ে পালিয়ে যায়। আর পাল-সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ মগধ অঞ্চলে বসে ষড়যন্ত্র করে।
বরেন্দ্রীর ভূমিপুত্রদের কাছে রাষ্ট্রনীতির চেয়ে মানবনীতি অনেক বড়। তাই দিব্যোক যুদ্ধে পরাজিত পাল-রাজার মহিষীদের, তাদের অমাত্যদের ও তাদের অনুরাগীদের কোন ক্ষতি হতে দেয়নি। বরঞ্চ তারা রাজ্য ত্যাগের অনুমতি চাওয়ায় দিব্যোক তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা ও সসম্মানে রাজ্য ত্যাগের অনুমতি দেয়। তারা তাদের সকল অলংকার, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা নিয়ে যায়। কিন্তু ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করে। তারা অলংকার ও মুদ্রাসমূহ রামপালের হাতে তুলে দেয়। ফলে ষড়যন্ত্রকারী রামপালের অস্ত্র তৈরি ও সৈন্য সংগ্রহের জন্য কোন অর্থের অভাব থাকে না।
বাঘ যেমন মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে সেই লোকালয় ছাড়তে চায় না। ঠিক তেমনই রামপাল হায়েনার মতো আবারও পাল-রাজ্যে আক্রমণ শানানোর সুযোগ খুঁজে। দিব্যোকের পর রুদোক এবং তারপর ভীম বরেন্দ্রীর নৃপতি-নেতা হয়। রামপাল আরও অনেক আর্য রাজ-রাজন্যদের সঙ্গে নিয়ে লক্ষাধিক রথী-অশ্বারোহী-পদাতিক ও হস্তীযুথ সৈন্যসহ বরেন্দ্রী আক্রমণের জন্য তৈরি হয়। আর ওদের জন্য পাল-রাজাদের অন্নভোগী ও কবিশ্রেষ্ঠ সন্ধ্যাকর নন্দী বীরগাঁথা রচনা করে। এই প্রতিভাবান কবিকে ‘কলিকালের বাল্মিকী’ বলা হয়। যার কাব্যে আগ্রাসী পাল-রাজাদের সঠিক ও কৈবর্তদের ধিকৃত হিসেবে বর্ণনা করা হয়। সে কৈবর্ত জাতি ও দিব্যোককে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ ও কুৎসাপূর্ণ কাব্য রচনা করে।
পপীপ রামশর্মার ইক্ষু ক্ষেতে আঠার বছর কাজ করে। সে প্রথমে মল্ল, ঊর্নাবতী ও পরে বাসুখুড়োর কাছে বিদ্যালাভ করে। যে অস্ত্রের নাম বর্ণমালা সে ওদের মাধ্যমে তা আয়ত্ব করে। সে বাসুখুড়োর কাছে বরেন্দ্রীর জন্মের ইতিহাস ও আর্যদের অত্যাচারের কথা শুনে। এসবই তার জীবনের পাথেয়। সে বট্যপের অনুমতিক্রমে রামশর্মার দাসত্ব থেকে পালিয়ে বরেন্দ্রীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পরান্নভোগী কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর বিপরীতে যৌক্তিক ও সত্যাসত্য লেখার জন্য সংস্কৃত-জ্ঞান লাভ করে ভূমিপুত্র কৈবর্ত-কবি পপীপ মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কিন্তু তার পথ-ঘাট অচেনা। দিনে বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে রাতের আঁধারে পথ চলে।
পপীপ পশু-পাখির চেয়ে পুরবাসী মানুষকে বেশি ভয় করে। কারণ তাকে ধরে আবারও রামশর্মার কাছে ফিরিয়ে দিলে পালানোর অপরাধে ভয়ানক শাস্তির পাশাপাশি অমানুসিক পরিশ্রমও করতে হবে। পুরবাসী মানুষকে ভয় করার পপীপের আরও কারণ আছে। ভিনদেশ থেকে আগত সংস্কৃত জানা সুসভ্য এই মানুষই ভূমি ও জনপদ কেড়ে নেয়, ওদের দাস বানায়, বন্দি করে রাখে, কয়েক কার্ষাপণ মুদ্রার বিনিময়ে মানুষের দেহ, আত্মা ও উত্তর-পুরুষকে কিনে নেয়।
পপীপ হাঁটতে হাঁটতে ভরদুপুরের খা খা রোদে উত্তপ্ত লাল মালভূমিতে এসে পৌঁছে। সে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। সে জ্ঞান হারায়। যখন তার জ্ঞান ফিরে তখন সে চোখ মেলে একজন পৌড়কে দেখতে পায়। সে গাঁয়ের মোড়ল হড়জন। যে তাকে সাদরে পানি মুখে তুলে দেয়। পপীপ বরেন্দ্রীর মাটিতে পৌঁচেছে শুনে উপুর হয়ে মাটিকে প্রণাম করে। সে নিজকে মুক্ত ভাবে। নিজ ভাষার মানুষের সন্ধান পেয়ে ওদের সবাইকে আপন মনে হয়। অথচ রামশর্মার ইক্ষু ক্ষেতে হাজার হাজার কৈবর্তরা সবাই দাস। এখানে মুক্ত। এখানে সে হড়জনের মুখে কট্টলির জন্মের ইতিহাস শুনে তার কবি প্রতিভাকে শানিত করে।
হড়জনের দুই মেয়ে কুরমি ও কুরচি। কুরমির সেবায় পপীপ সুস্থ হয়ে উঠে। এই কুরমিকে দেখে পপীপের সুপ্ত যৌবন সাড়া দেয়। কিন্তু মানকুর সঙ্গে কুরমির বিয়ের দিন-ক্ষণ ঠিক হয়ে আছে। পপীপ মায়ের সন্ধানে দেদ্দাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে হড়জনের গ্রাম ঘুরতে বেরোয়। ঘুরতে ঘুরতে সে এক সময় এক পুকুরের ধারে আসে। সেখানে কুরমিকে স্নানরত দেখে সে থমকে দাঁড়ায়। কুরমি তাকে আহবান জানায়। সে পানিতে নামে এবং কুরমির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হয়। যখন পপীপ দেদ্দাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয় তখন কুরমি তার অপেক্ষায় থাকার জন্য কথা দেয়।
পপীপ দেদ্দাপুরে রওনা হয়ে পথে একজন অদ্ভুতদর্শন যোগীর দেখা পায়। তার নাম তিলোঁ। সে এক মহান কবি। তার কাছে সে ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈনদের সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। সেসব নিয়ে সে তার স্বজাতি অর্থাৎ ভূমিপুত্রদের গৌরবগাঁথা রচনা করতে উদগ্রীব হয়। সে দেদ্দাপুরে ফিরে তার মাকে খুঁজে পায় না। সে মল্ল ও ঊর্ণাবতীর দেখা পায়। মল্ল তাকে ঘোড়ায় চড়া শেখায়। সে একদিন ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে ঘুরতে এক আর্য-গ্রামে প্রবেশ করে। আর্য-গ্রাম মানেই কৈবর্তদের কাছে দেবগ্রাম। সেখানে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষেধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ গণ্য হলেও সে গাঁয়ে বৃদ্ধরা তাকে সমীহ করে। কারণ এখন তারা ভীমের দ্বারা শাসিত। পপীপ মনে মনে হাসে আর ভাবে, এই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ যদি আগে থাকতো!
আগে মল্ল’র কোন ঘর ছিল না। সে যেখানে রাত সেখানে কাত হতো। কিন্তু সে এখন অট্টালিকায় বাস করে। এটা ভীম তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। সেখানে গিয়ে পপীপ ঊর্ণাবতীর দেখা পায়। এতে সে অবাক হয়। কারণ সে দেবতার আশ্রয় ছেড়ে মল্ল’র কাছে এসেছে। ঊর্ণাবতী আর্য ধর্ম সম্পর্কে বিষোদগার করে পপীপকে বলে, যে ধর্ম শাস্ত্রের বিধান দিয়ে আমাকে দেবদাসী বানিয়েছিল সেটি কোন মানুষের পালনীয় ধর্ম হতে পারে কি! তুই জানিস দেবদাসী মানে কি। যে ধর্ম আমাকে দেবদাসী বানিয়েছে আমি সেই ধর্ম পালন করবো, নাকি যে ধর্ম আমাকে দেবদাসীর কলুষিত জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছে আমি সেই ধর্ম পালন করবো!
মল্ল পপীপকে রাজধানীতে ভীমের কাছে নিয়ে যায়। ভীম এই কৈবর্ত কবি’র জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। মল্ল পপীপকে বলে, ‘ভীমের যুদ্ধ রামপালের সঙ্গে আর তোর যুদ্ধ এই সন্ধ্যাকর নন্দীর সঙ্গে। আর্য-দস্যুদের যেমন লেখনি-সহায় সন্ধ্যাকর নন্দী, তেমনই কৈবর্ত জাতির লেখনি-সহায় হতে হবে পপীপকে’। মূলত বরেন্দ্রীর ভূমিপুত্ররা যুগের পর যুগ সন্ধ্যাকর নন্দীর মতো একজন কবি’র প্রতীক্ষায় আছে যে তাদের পূর্ব-পুরুষের বীরগাঁথা উত্তর পুরুষের জন্য খাগের লেখনিতে ভূর্যপত্রে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করে যাবে। আর মল্ল পপীপকে এ কথাটিও বোঝানোর চেষ্টা করে যে বর্ণ বা অক্ষরের শক্তিই সবচেয়ে বড় ব্রহ্মাস্ত্র।
রামপাল অপরের সাহায্য-সহযোগিতায় অনেক শক্তি সঞ্চয় করে। তার সঙ্গে এগারজন সামন্ত রাজা যোগ দেয়। এসব খবর পেয়ে ভীমের পরামর্শক পদ্মনাভ ও সেনাপতি হরিবর্মার কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ে। রামপালের চতুরঙ্গ সৈন্য থাকলেও ভীমের একমাত্র সহায় তার কৈবর্ত যোদ্ধারা। তারা বন্য মহিষ ধরে এনে অশ্বারোহীর বিপরীতে প্রশিক্ষণ দেয়। কিন্তু বৌদ্ধ মহাবিহার থেকে প্রায়শই কৈবর্তদের বরেন্দ্রীতে গুপ্ত হামলা চালিয়ে অনেককে হত্যা করা ও বাড়ি ঘরে অগ্নি সংযোগ করা হয়। এটা টের পেয়ে ভীমের নেতৃত্বে মহাবিহার ঘেরাও করা হয়। এতে পপীপও অংশগ্রহণ করে। অবশেষে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অপরাধীদের ভীমের সেনাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়।
রামপাল যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং কৈবর্তদের নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করছে তখন রাজবংশী বরেন্দ্রীদের সঙ্গে কৈবর্তদের একটু বোঝা-পড়ার প্রয়োজন হয়। অবশেষে রাজবংশীরাও কৈবর্তদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। কারণ ওরাও জানে এই যুদ্ধে পরাজয় মানে আর্যদের অধীন হতে হবে। আর সেক্ষেত্রে তারা ধন-সম্পদের অধিকারী হবে না, পূজায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না, ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে পারবে না, আর্যদের বিরুদ্ধে ওদের কোন অভিযোগ আমলে নেওয়া না হলেও আর্যদের যে কোন অভিযোগের প্রমাণ ছাড়াই ওরা দণ্ডিত হবে। ওদিকে কোচ, শবর ও ভিল জাতির মোড়লরা আগেই এই যুদ্ধে যেতে সম্মত হয়েছিল।
পপীপ কাব্য রচে। সে ঋতকে পৃথিবীর পরিচালক রূপে কল্পনা করে। তার আমলে সবাই সুখে-শান্তিতে বসবাস করে। তখন মানুষ বলতো, ‘আমার’। তখন তারা ‘আমাদের’ বলতে জানতো না। সেই ঋতকে ইন্দ্র ধ্বংস করায় পৃথিবীতে বৈষম্যের অভিশাপ নেমে আসে। ঋত বলেছিল ওলান ঠাকুরের আশীর্বাদে বরেন্দ্রীতে একজন দিব্যোকের জন্ম হবে। তখন মানুষ অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে। এসব কবিতা শুনে ঊর্ণাবতী ও মল্ল খুশি হয়। পপীপ তখন মল্ল, ঊর্ণাবতী ও বাসুখুড়োর প্রসংশা করে ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। প্রত্যুত্তরে ঊর্ণাবতী বলে, কেউ কাউকে কবিতে রূপান্তর করতে পারে না। কবি হয়েই কবি জন্ম নেয়।
ঘোড়া ছুটিয়ে পপীপ কুরমির কাছে যায়। কিন্তু ঘোড়া থেকে নামার আগেই কুরমির কপালে সিঁদুর দেখে সে মুষড়ে পড়ে। সে ভাবে মানকুর সঙ্গে কুরমির বিয়ে হয়েছে। এখানে বেশ নাটকীয়তার পর পপীপ জানতে পারে আসলে ওর সঙ্গেই কুরমির বিয়ে হয়েছে। কারণ কুরমির সঙ্গে ওর শারীরিক সম্পর্কের বিষয়টি কুরমি কুরচিকে জানায়। কুরচি তার মাকে জানায়। তার মা হড়জনকে জানায়। হড়জন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায়ে মানকুর বাবাকে জমি-জমা দণ্ড দিয়ে ক্ষমা চায়। এসব শুনে পপীপের মন থেকে সকল হতাশা দূর হয়ে যায়। সে আকাশের চাঁদ হাতে পায়। সে কুরমির জন্য পাগল হয়ে যায়। সে ভূর্যপত্রে খাগের লেখনিতে তার লিখিত শ্লোক ও কবিতাগুলো কুরমির কাছে গচ্ছিত রেখে যুদ্ধে শরিক হওয়ার জন্য রওনা হয়।
ভীমের কাছে রামপাল চরম পত্র পাঠায়। সে ভীমকে বশ্যতা স্বীকার করতে অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলে। বরেন্দ্রীর কৈবর্তদের সর্বসম্মতিক্রমে ভীম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। যুদ্ধের ময়দানে ভূমিপুত্রদের সাহস দেখে পপীপ অবাক হয়। প্রথমে রামপালের সেরা যোদ্ধা মুকুন্দে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য ভীম বাহিনীর একজনকে আহবান জানায়। ওলান ঠাকুরের নামে কালো মোরগ বলির পালক দ্বারা সেই দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য পনের বছর বয়সী ‘বিজু’ মনোনীত হয়। ওকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করলেও মুকুন্দে ধরাশায়ী হয়। এরপর পাঁচজনের দল দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহবান জানায়। সেখানেও রামপালের সৈন্যরা পরাজিত হয়। তারপর শুরু হয় সর্বাত্মক যুদ্ধ। সেখানে ওদের অশ্বারোহী বাহিনীকে চমকে দিয়ে বিশাল কালোমেঘের মতো মহিষারোহী বাহিনী হামলে পড়ে। রামপালের বাহিনী পর্যদুস্ত হয়ে পড়ে এবং রাত্রি নেমে আসে। এসব দেখে আর পপীপ ওদের বীরগাঁথা রচনা করে।
যুদ্ধের শর্তানুসারে রাতে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। এটা রামপালের পক্ষ থেকে তার সেনাপতি কাহ্নুর দেবের শর্ত ছিল। কিন্তু তারাই শর্ত ভঙ্গ করে রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত কৈবর্তদের তাবুতে আগুন দেয় এবং নির্বিচারে তাদের হত্যা করতে থাকে। তখন ভীমের মনে পড়ে তার পিতৃব্য দিব্যোক এবং পিতা রুদোক তাকে সাবধান করে বলেছিল, ‘সাপ, হায়েনা আর পালরাজ্যের অমাত্যদের বিশ্বাস করতে নেই’। ভীম বিলাপ করতে থাকে। এই বর্বরোচিত হামলার নায়ক সেনাপতি কাহ্নুর দেবকে মল্ল দেখতে পায়। সে তাকে হত্যার শপথ করে। ওদিকে এ বিভৎস দৃশ্য দেখে পপীপ ভেঙ্গে পড়ে। সে খাগের লেখনি ও ভূর্যপত্র ফেলে অস্ত্র হাতে শত্রু নিধনে মেতে উঠে।
উগ্র, মল্ল এবং অন্যান্যরা প্রাণপণ যুদ্ধ করে। মল্ল কাহ্নুর দেবকে হত্যা করতে সমর্থ হয়। রামপালের সেনারা মল্লকেও হত্যা করে। অসম যুদ্ধ শেষ হয়। ভীম ও ভীমের যোদ্ধারা কেউ বেঁচে নেই। ভীম, উগ্র আর পপীপের দেহে এতো তীর বিঁধেছে যে দেখে মনে হয় বিশাল তিনটি সজারু উপুর হয়ে পড়ে আছে। বিজয়ী রামপাল তার প্রিয় হস্তী বাদলের পিঠে উঠে যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনে আসে। ভীমের মৃতদেহ না দেখে সে তার বিজয় নিশ্চিত হতে পারে না। রামপাল ভীমের কাছে আসে। সে তখনও মরেনি। রামপালকে দেখে ভীমের মুখে আশ্চর্য এক হাসি ফুটে। সে রামপালকে বলে, তুই বলেছিলি তুই অর্জুনের বংশধর। তুইও একটি জারজ। তোদের মুখের কথার ঠিক নেই। এ কথাটি জানানোর জন্যই বেঁচে আছি।
রামপাল ক্রোধে কাঁপতে থাকে। সে নিজকে পরাজিত মনে করে। সে মাহুতকে আদেশ করে যেন হাতির পায়ের নীচে ভীমকে পিষ্ট করা হয়। বাদলও মানুষকে পায়ের নীচে পিষ্ট করে আনন্দ পায়। বাদল ভীমকে পিষ্ট করে। রামপাল ঘোষণা করে কৈবর্তদের মৃতদেহ সৎকার করা যাবে না। এরা যুদ্ধক্ষেত্রেই পড়ে থাকবে। ওদের মৃতদেহ শেয়াল-শকুন খাবে।
সেই প্রতারণাপূর্ণ যুদ্ধের রাত্রির ভোর হয়। যুদ্ধের ময়দানে সারাদিন কৈবর্তদের লাশ পড়ে থাকে। পরের রাতে মশাল প্রজ্জলিত করে লাখো কৈবর্ত নারী-বৃদ্ধ-শিশু যুদ্ধক্ষেত্রে স্বজনের সন্ধানে এগিয়ে যায়। তাদের নেতৃত্ব দেয় ঊর্ণাবতী। ওরা সবাই বিলাপের সুর তুলে। ওদের বিলাপে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠে। তারা এক অভিন্ন চিতায় প্রিয়জনদের সৎকার করার উদ্যোগ নেয়। সেই অভিন্ন চিতায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে। সেই অলৌকিক চিতার ধোঁয়া কুণ্ডুলি পাকিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাতের ভাস্কর্যের রূপ নিয়ে আকাশপানে উঠে এবং হিমালয়কে অতিক্রম করে যায়। সেটা পৃথিবীকে জানায়, আবার আমি আসবো। হাজার বছর পরে হলেও আসবো। এই জাতির মুক্তি হয়ে ফিরে আসবো। এক হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের অবতারণার মাধ্যমে এই উপন্যাসের সমাপ্তি টানা হয়েছে। নিজের অগোচরে কপোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।
#শেষকথা: ধর্ম কি? আমার দৃষ্টিতে ইহলৌকিক সার্বিক কল্যাণ এবং পারলৌকিক মুক্তির যে সোপান- তাই ধর্ম। যে বিধান নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অধিকার সুনিশ্চিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে- তাই ধর্ম। ধর্ম প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় নয়। বরঞ্চ ধর্ম দৈনন্দিন জীবনে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্টীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুবিস্তৃত। ধর্ম মানুষের মাঝে বিভেদ দূর করে। একমাত্র ধর্মই মানুষকে জাত-পাতের ঊর্ধ্বে বিবেচনা করে। ধর্ম এমন এক নিক্তি যাতে কালো-ধলো, আর্য-অনার্য, আরব-অনারব, এশিয়ান-ইউরোপিয়ান-আফ্রিকান সকল মানুষের ওজন সমান।
ধর্ম কখনও শোষণ, উৎপীড়ন, বঞ্চনা ও দাসত্বের হাতিয়ার হতে পারে না। বরঞ্চ ধর্মই মানুষকে শোষণ, নিপীড়ন, বঞ্চনা ও দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্তি দেয়। নারী ও অর্থ দুটোই বিশ্ব শান্তির মূল উৎস। এদের যথেচ্ছাচার ব্যবহারই বিশ্ব শান্তির অন্তরায়। নারী কখনওই ভোগ্য পণ্য হতে পারে না। ধর্ম নারীর সবচেয়ে বড় সুরক্ষা কবচ। ‘মানবাধিকার’ ও ‘মানব ধর্মের’ প্রবক্তাগণ নারীকে সুরক্ষা দিতে পারেনি। এই উপন্যাসে স্বধর্মের অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ঊর্ণাবতীর প্রতিটি কথাই প্রণিধান যোগ্য। তার মতে ধর্মীয় কোন অনুশাসন মানুষের অধিকার হরণ, মানবাধিকার লংঘন, নিপীড়ন ও নিষ্পেষণ যন্ত্র হতে পারে না।
আমি নিজের ধর্ম সম্পর্কে যৎসামান্যই জানি। অপরের ধর্ম সম্পর্কে কিচ্ছু জানি না। ওতে আমার আগ্রহ নেই এবং আমি কখনও অপরের ধর্ম নিয়ে কথা বলি না। কিন্তু এই উপন্যাসটিতে আমি যেসব বর্ণনা পেয়েছি তা এক কথায় অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। এর কিছু কথা আগে অনেকের মুখে শুনলেও এবার পড়লাম। আমার মতে এসব কোন ধর্মীয় বিধান হতে পারে না। আগের যুগের নিরক্ষর মানুষ নাহয় সেসব মেনে নিয়েছে। কিন্তু বর্তমানের শিক্ষিত মানুষও কি এসব নিয়ে কথা বলে! বলতে শুনিনি। তাছাড়া বৌদ্ধ ধর্মের মানুষও যে এমন অমানুষ হতে পারে তা আমি রোহিঙ্গাদের প্রতি মায়ানমারের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অমানবিক আচরণ দেখার আগে বিশ্বাস করিনি। কারণ এই ধর্মে প্রাণি হত্যা মহাপাপ। অথচ ওরাই অবলীলায় মানুষ হত্যা করে।
ধর্ম মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তির জন্য। কিন্তু যদি ধর্ম মানুষের ইহকালীন অশান্তি ও পারলৌকিক ধ্বংসের কারণ হয় সেটা কোন ধর্ম হতে পারে না। তাছাড়া ধর্মই দাস-প্রথা উচ্ছেদ করেছে। কোন জাতি ধর্মকে ব্যবহার করে মানুষকে সেবাদাস ও দেবদাসী বানাতে পারে না। তাহলে সেটা ধর্মের মর্যাদা হারায়। অথচ এমন অনেক বাক্য এই উপন্যাসে রয়েছে যা ধর্মকে ব্যবহার করে মানুষকে মুক্তি না দিয়ে তাদের দাসে পরিণত করেছে এবং শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনার বড় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।
উপন্যাসটিতে অনেক অশ্লীল কথা-বার্তা ও ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। সবই ধর্মগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। আমার লেখায় আমি সেসব এড়িয়ে গেছি। কারণ আমি আমার কোনও লেখায় এসব শব্দ ব্যবহার করি না। এতে শ্রদ্ধাভাজন লেখককে আমি দোষারোপ করছি না। কারণ এসব কথা তিনি অত্যাবশ্যকীয়ভাবে তার উপন্যাসে ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন।
উপন্যাসটিতে বড় বড় অনেক অনুচ্ছেদ রয়েছে। কোন কোন অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে। এটা কখনও বা পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিছু বানান ভুল ও নগণ্য পরিমাণ মুদ্রণ প্রমাদ চোখে পড়েছে। আর সার্বিক বিচারে বইটি এতো ভালো লেগেছে যে সবাইকে পড়ার অনুরোধ করছি। এমন একটি উপন্যাস রচনার জন্য লেখককে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি আরও এমন উপন্যাস রচনার জন্য আশীর্বাদ করছি।
পিতৃগণ ক্ষেত্রে লেখকের পরিশ্রম ও সাধনার কথা ভেবেই আমার মাথা ঘুরে। আসলেই এমন জ্ঞান-গর্ভ লেখার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আরাম-আয়েশ থেকে নিজকে বঞ্চিত করতে হয়। জনাব জাকির তালুকদার-এর ‘পিতৃগণ’ লেখার জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্তে কায়িক ও মানসিক শ্রমের পাশাপাশি প্রচুর অর্থ ব্যয়ও করেছেন। কারণ এই উপন্যাস লেখার আগে অনেক দূর-দূরান্তে ঘুরেছেন, অনেকের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং অনেক ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন।
পিতৃগণ উপন্যাসের লেখক সত্য ও সুন্দরের অনুসারী। প্রকৃত ও সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য সদা তৎপর ও অকুতোভয় সৈনিক। তার প্রতি আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণের অসীম শ্রদ্ধাঞ্জলি। তার পুণ্যময় হায়াতের প্রার্থনা করছি এবং ভুল-ত্রুটির জন্য তার ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টির প্রত্যাশা করছি।